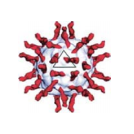পোলিও ভাইরাস
| পোলিও ভাইরাস | |
|---|---|

| |
|
TEM micrograph of poliovirus virions. Scale bar, 50 nm. | |

| |
| একটি টাইপ থ্রি পোলিওভাইরাস যা ক্যাপসিড চেইন দ্বারা রঙিন। | |
| ভাইরাসের শ্রেণীবিন্যাস | |
| গ্রুপ: | ৪র্থ গ্রুপ ((+)ssRNA) |
| বর্গ: | Picornavirales |
| পরিবার: | Picornaviridae |
| গণ: | Enterovirus |
| প্রজাতি: | Enterovirus C |
| Subtype | |
|
Poliovirus | |
পোলিও ভাইরাস (ইংরেজি: Poliovirus) হলো একধরনের এন্টারোভাইরাস ও পিকর্নাভাইরিডি পরিবারের সদস্য। এটা মানব শরীরে পোলিওমায়েলাইটিস রোগ সৃষ্টি করে যা সাধারণত পোলিও নামে পরিচিত। পোলিও ভাইরাস একটি আরএনএ (RNA) জিনোম ও একটি প্রোটিন ক্যাপসিড নিয়ে গঠিত। এর জিনোমটি একসূত্রক পজিটিভ সেন্স আরএনএ (RNA) জিনোম যা ৭৫০০ নিউক্লিওটাইড নিয়ে গঠিত। ভাইরাস কণাটি আইকোসাহেড্রাল ও ৩০ ন্যানোমিটার ব্যাস বিশিষ্ট।
কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার ও আরউইন পপার ১৯০৯ সালে প্রথম পোলিও ভাইরাস পৃথক করেন। ১৯৮১ সালে ভিনসেন্ট রাকানিল্লো ও ডেভিড ব্যাল্টিমোর ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি নামক প্রতিষ্ঠানে ও নওমী কিতামুরা এবং ইকার্ড উইমার স্টোনি ব্রুক বিশ্ববিদ্যালয়ে পোলিও ভাইরাস জিনোম প্রকাশ করেন। পোলিও ভাইরাস খুবই সুগঠিত ভাইরাস হওয়ায় এটি আরএনএ ভাইরাস নিয়ে গবেষণায় আদর্শ ভাইরাস হিসেবে বিবেচিত হয়।
বৈশিষ্ট্য
পোলিও ভাইরাস হচ্ছে এন্টারোভাইরাস গ্রুপের সদস্য। এন্টারোভাইরাসগুলো ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রেপ্লিকেশন বা বংশবৃদ্ধি করতে পারে। এরা অ্যাসিড সহনশীল হওয়ায় পাকস্থলীর অ্যাসিডিক পরিবেশে টিকে থাকতে পারে। পোলিও ভাইরাসের পোষক শুধু স্তন্যপায়ী প্রাণী হয়ে থাকে। এর কারণ হলো এর ভাইরাল ক্যাপসিড প্রোটিন শুধু এমন এক রিসেপ্টরের সাথে বন্ধন করে যা কেবল স্তন্যপায়ী প্রাণীর কোষঝিল্লিতে বিদ্যমান। পোলিও ভাইরাস আবরণবিহীন ভাইরাস হওয়ায় পরিবেশে দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারে ফলে মল বা দূষিত পানি ও খাবারের মাধ্যমে ছড়াতে পারে। বাহ্যিক ক্যাপসিডের অ্যান্টিজেনিক বৈচিত্র্য অনুযায়ী তিনটা সেরোলজিক টাইপের পোলিও ভাইরাস পাওয়া যায় (PV1, PV2, PV3)।
রেপ্লিকেশন

ভাইরাসের বংশবৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে রেপ্লিকেশন বলে। কোষঝিল্লিতে অবস্থিত CD155 রিসেপ্টর (পোলিও ভাইরাস রিসেপ্টর) এর সাথে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে কোষে প্রবেশ করে। এবং ক্যাপসিড প্রোটিন দূরীভূত হয়। পোলিও ভাইরাস পজিটিভ সেন্স RNA ভাইরাস হওয়ায় এর জিনোম mRNA হিসেবে কাজ করে এবং ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি দীর্ঘ পলিপেপটাইড তৈরি করে যাকে নন-ক্যাপসিড ভাইরাল প্রোটিন বলে।
একটি ভাইরাস-এনকোডেড প্রোটিয়েজ উক্ত পলিপেপটাইডকে কয়েক ধাপে ভেঙে পোজেনি ভিরিওন এর ক্যাপসিড প্রোটিন, কিছু নন-ক্যাপসিড প্রোটিন ও RNA পলিমারেজ এনজাইম তৈরি করে যা প্রোজেনি RNA জিনোম সংশ্লেষণে ভূমিকা রাখে।
জিনোমের রেপ্লিকেশন হয় একটি পরিপূরক নেগেটিভ স্ট্রান্ড সংশ্লেষণের মাধ্যমে যা পজিটিভ স্ট্রান্ড তৈরিতে টেম্পলেট বা ছাঁচ হিসেবে কাজ করে। ক্যাপসিড প্রোটিনের দ্বারা জিনোম RNA আবরিত হওয়ার মাধ্যমে প্রোজেনি ভিরিওনগুলো একত্রিত হয়। কোষীয় সাইটোপ্লাজমে ভিরিওনগুলো একত্রিত হয় এবং কোষের মৃত্যুর পর অবমুক্ত হয়।
বিস্তার
মানুষ হলো একমাত্র প্রাকৃতিক পোষক। পোলিও মানব দেহের ওরোফ্যারিংস ও ইন্টেস্টিনাল ট্রাক্টে বংশ বৃদ্ধি করতে পারে। এরা ফিকাল-ওরাল রুটে ছড়ায় অর্থাৎ মানুষের মলের মাধ্যমে পরিবেশে ছড়ায় এবং সেখান থেকে দূষিত খাবার ও পানির মাধ্যমে আরেকজনের দেহে প্রবেশ করে। একবার পোলিওতে আক্রান্ত হওয়ার পর কয়েক মাস পর্যন্ত মলের মাধ্যমে এই ভাইরাস নির্গত হতে থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০০৫ সালের মধ্যে প্যারালাইটিক পোলিও দূর করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ২০০৭ সালেও ১৬ টি দেশে পোলিওর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ১৯৮৮ সালে সারাবিশ্বে ৩,৮৮,০০০ পোলিও রোগী ছিল যেখানে ২০০৫ সালে তা কমে প্রায় ২০০০ জনে নেমে আসে। গুটিবসন্ত একমাত্র সংক্রামক ব্যাধি যা টিকার মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হয়েছে। ২০১৪ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশ, ভারতসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ১১ টি দেশ কে পোলিও মুক্ত ঘোষণা করে।
রোগ
সুপ্তাবস্থা সাধারণত ৭-১৪ দিন। পোলিও ভাইরাস সংক্রমণের চার ধরনের অবস্থা পরিলক্ষিত হয় যেমন-
- সুপ্তাবস্থা বা উপসর্গবিহীন সংক্রমণ
উপসর্গবিহীন সংক্রমণের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। প্রায় এক শতাংশ ক্ষেত্রে লক্ষণ প্রকাশ পায়।
- অ্যাবর্টিভ পোলিওমায়েলাইটিস
ক্লিনিক্যাল প্রেক্ষাপটে অ্যাবর্টিভ পোলিওমায়েলাইটিসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এতে হালকা জ্বর, মাথাব্যথা, গলাব্যথা, বমিভাব, বমন হতে পারে। অধিকাংশ রোগী এমনিতেই ভালো হয়ে যায়।
- নন-প্যারালাইটিক পোলিওমায়েলাইটিস
এক্ষেত্রে রোগীর অ্যাসেপ্টিক মেনিনজাইটিস হয় যার ফলে জ্বর, মাথাব্যথা, ঘাড় শক্ত হয়ে যায়। এধরনের রোগীরাও এমনিতেই ভালো হয়ে যায়।
- প্যারালাইটিক পোলিওমায়েলাইটিস
এই রোগে মাংসপেশি দুর্বল হয়ে যায়। মটর স্নায়ু স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে অন্যান্য স্নায়ুকোষ সক্রিয় হওয়ার ফলে মাংসপেশির কার্যক্ষমতা কিছুটা পুনরুদ্ধার হতে পারে। ব্রেইন স্টেম আক্রান্ত হলে রেস্পিরেটরি মাসল প্যারালাইসিস হতে পারে যা এই রোগে মৃত্যুর অন্যতম কারণ।
প্যাথজেনেসিস
পোলিও ভাইরাস ওরোফ্যারিংস ও ক্ষুদ্রান্ত্রের লিম্ফয়েড টিস্যুতে রেপ্লিকেশন করে। অতঃপর সেখান থেকে রক্তের সংস্পর্শে এসে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে পৌছায়। নার্ভ অ্যাক্সনের মধ্য দিয়েও ছড়াতে পারে। এরা স্পাইনাল কর্ডের অ্যান্টেরিওর হর্ন কোষে অবস্থিত মটর নিউরনে রেপ্লিকেশন করে। আস্তে আস্তে উক্ত কোষগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ফলে উক্ত নিউরনগুলো যে সমস্ত মাংসপেশিকে স্নায়ু উদ্দীপনা প্রদান করত তারা প্যারালাইসিস বা অবশ হয়ে যায়। মাংসপেশিতে ভাইরাস সংক্রমণের জন্য প্যারালাইসিস হয় না। ভাইরাস ব্রেইন স্টেম কেও আক্রান্ত করতে পারে ফলে বালবার পোলিওমায়েলাইটিস হয়।
শনাক্তকরণ
কণ্ঠনালি, মল বা স্পাইনাল ফ্লুইড থেকে সেল কালচার করে ভাইরাস পৃথকীকরণ সম্ভব। অ্যান্টিবডি টাইটারের বৃদ্ধি পরিমাপ করেও রোগ নির্ণয় করা সম্ভব।
টিকা
পোলিও ভাইরাসের বিরুদ্ধে দুই ধরনের টিকা বিদ্যমান।
- সল্ক ভ্যাকসিন (Salk vaccine), অপরনাম কিল্ড ভ্যাকসিন বা নিষ্ক্রয় টিকা (IPV)।
- সেবিন ভ্যাকসিন (Sabin vaccine), অপরনাম লাইভ অ্যাটেনুয়েটেড ভ্যাকসিন, ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন (OPV)
দুটি টিকায় তিনটি সেরোটাইপ রয়েছে। উভয় টিকায় হিউমোরাল অ্যান্টিবডি তৈরি করে যা রক্তে প্রবেশকৃত ভাইরাস কে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে, ফলে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র রক্ষা পায় এবং রোগ প্রতিরোধ হয়। পোলিও মূলোৎপাটনে লাইভ ভ্যাকসিন বেশি কার্যকর তাই ভারতীয় উপমহাদেশে মনোভ্যালেন্ট ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন ব্যবহার করা হয়।
তবে লাইভ ভ্যাকসিনের কিছু অসুবিধা রয়েছে যেমন:
- যদিও বিরল, কখনো কখনো অ্যাটেনুয়েটেড ভাইরাস সক্রিয় হয়ে রোগ সৃষ্টি করতে পারে।
- কম রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিশিষ্ট ব্যক্তিকে এই টিকা দেওয়া যায় না কারণ এটা তাদের শরীরে রোগ সৃষ্টি করে।
- অন্ত্রে অন্য এন্টারোভাইরাস সংক্রমণ করলে পোলিও ভাইরাসের রেপ্লিকেশন কমে যায়, ফলে টিকার কার্যকারিতা কমে যেতে পারে।
- অধিক তাপমাত্রায় এই টিকার কার্যকারিতা কমে যায় তাই এটাকে বাধ্যতামূলকভাবে ফ্রিজে রাখতে হয়।
ওরাল পোলিও ভ্যাকসিনের একটি সুবিধা হচ্ছে এটি অন্ত্রে সিক্রেটরি ইমিউনোগ্লোবিউলিন -এ (IgA) তৈরি করে যা ভিরুলেন্ট (রোগ সৃষ্টিকারী) পোলিও ভাইরাস কে নিষ্ক্রিয় করে এবং রোগীর দেহ থেকে অন্যের শরীরে ছড়ানো রোধ করে। এর ফলে একটি সম্প্রদায়ের একাংশ কে টিকা প্রদানের মাধ্যমে পুরো সম্প্রদায়ের সমগ্র জনগণ কে রোগের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব যা হার্ড ইমিউনিটি (Herd immunity) নামে পরিচিত।
বহিঃসংযোগ
- ICTVdb virus classification 2006
- Home of Picornaviruses (latest updates of species, serotypes, & proposed changes) ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ৪ নভেম্বর ২০১০ তারিখে
- Goodsell, David। "Poliovirus and Rhinovirus"। August 2001 Molecule of the Month। ৩ মার্চ ২০১১ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৩০ জানুয়ারি ২০২১।
- 3D macromolecular structures of the Poliovirus archived in the EM Data Bank(EMDB)
- "Human poliovirus 1"। NCBI Taxonomy Browser। 12080।
- "Human poliovirus 3"। NCBI Taxonomy Browser। 12086।